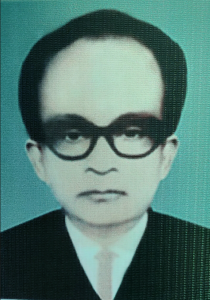
আসাদুজ্জামান খান (১৯১৬—২১ জানুয়ারি ১৯৯২)
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাঁর মামাতো ভাই আসাদুজ্জামান খানকে বড় ভাই ফজলুল করিম খান রসিকতা করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘নজরুল তো মন্ত্রী হইছে। তুই মন্ত্রী হইলে যাইতি না মিন্টু রোডে?’ আসাদুজ্জামান খান তখন ময়মনসিংহ-২৬ আসনের সংসদ সদস্য এবং এর আগে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেও ছিল তাঁর হৃদ্যতা। বড় ভাইয়ের রসিকতার জবাবে আসাদুজ্জামান খান বললেন, ‘আমি মিন্টু রোডে যাইতাম না।’ বড় ভাই জিজ্ঞেস করলেন- ক্যারে? তিনি জবাব দেন: ‘ভাইছাব হুনেন, আমি যদি ওইহানে (মিন্টু রোড) যাই, আবার আয়া পড়তে অইব বিছনা-বেডিং নিয়া। এহানেই থাকবাম।’
আসাদুজ্জামান খানের বাড়ি তখন রাজধানীর সেগুন বাগিচা এলাকায় ২৪/এ তোপখানা রোডে। বড় ভাইকে বললেন: ‘যদি মন্ত্রী হই, ওইহানে, বাড়ির কোণাডায় একটা পুলিশ বক্স বানাইবো। মন্ত্রিত্ব গেলে গা পুলিশ থাকব না। কিন্তু বক্সটা থাকব। মানুষ তখন কইব, ওই যে মন্ত্রীর বাড়ি।’ যদিও শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ পাটমন্ত্রী হয়েছিলেন আসাদুজ্জামান খান। উল্লেখ্য, আসাদুজ্জামান খান মোট তিনবার মন্ত্রী পদমর্যাদায় ছিলেন। কিন্তু কখনো মিন্টু রোডে সরকারি বাড়িতে ওঠেননি। তিনি সব সময় তোপখানা রোডে নিজের বাড়িতেই ছিলেন।
বঙ্গবন্ধু ১১৫ জন সদস্যকে নিয়ে বাকশালের যে কেন্দ্রীয় কমিটি করেছিলেন, সেখানে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ১৪ জন সদস্য ছিলেন। আসাদুজ্জামান খান তাঁদের অন্যতম। তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পরে বন্দুকের নলের মুখে তিনি খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বাধ্য হন। তাঁকে দেয়া হয়েছিল বন্দর ও জাহাজ চলাচল বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

কিশোরগঞ্জ শহরে আসাদুজ্জামান খানের জন্মভিটা (জুলাই ২০২৪)
আসাদুজ্জামান খান (গণপরিষদের ডকুমেন্টে নামের বানান আছাদুজ্জামান খান) ১৯১৬ সালে (সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়নি) কিশোরগঞ্জ শহরের আখড়াবাজার এলাকায় বিখ্যাত কাজীবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আব্দুল হাকিম খান ‘কাজী সাহেব’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন পেশায় একজন কাজী বা বিচারক। সম্ভ্রান্ত মানুষ ছিলেন। ব্রিটিশ আমলেই তিনি কিশোরগঞ্জের মতো ছোট্ট শহরে টেনিস খেলতেন। আসাদুজ্জামান খানের মায়ের নাম নুরজাহান বেগম। এই দম্পতির তিন ছেলে এক মেয়ে। আসাদুজ্জামান খান সবার ছোট। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, জাতীয় নেতা ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি জহুরুল ইসলাম তাঁর মামাতো ভাই।
আসাদুজ্জামান খান কিশোরগঞ্জ রামানন্দ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে পড়ালেখার জন্য কলকাতায় চলে যান। সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স, মাস্টার্স এবং বি.এল (ব্যাচেলর অব ল) ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর জীবনে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণি নেই। বরাবরই প্রথম হয়েছেন।
সরকারি চাকরি ছেড়ে আইনজীবী
আসাদুজ্জামান খানের বড় ভাইয়ের ছেলে কাজী সেলিম খান জানান, তিনি ১৯৪১ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। জুডিসিয়াল সার্ভিসে বছর পাঁচেক চাকরি করেন। তিনি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপের মুন্সেফ ছিলেন। ১৯৪৫ সালে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৯৪৫ সনে ঢাকা হাইকোর্ট বারে এবং পরে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের খন্ডকালীন শিক্ষক পদে যোগ দেন এবং হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। কালক্রমে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।
১৯৬৯-৭০ সময়ে ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি তিনি দুই মেয়াদে (৩ জুন ১৯৭২ থেকে ৩০ জুন ১৯৭৩ এবং ১ জুলাই ১৯৭৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫) ঢাকা বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেরও (বর্তমানে সিণ্ডিকেট) সদস্য ছিলেন।
পাকিস্তান আমলেই বিরোধী নেতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি হলেও রাজনীতিতে সেভাবে সক্রিয় ছিলেন না। মূলত পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তবে ১৯৬৫ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর এলাকা থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর ১১ জুন পরিষদে স্বতন্ত্র দল গঠন করে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালের ১২ অক্টোবর পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সংসদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এ দলের প্রার্থী হিসেবে ময়মনসিংহ-১৫ (জাতীয় পরিষদ ৯০) আসন থেকে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মূলত বঙ্গবন্ধু তাঁর মেধা ও প্রজ্ঞার কারণে তাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৮৩২ জন। আসাদুজ্জামান খান পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৮৩৭ ভোট। (নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও ফলাফল, ঐতিহ্য/২০২৩, পৃ. ২৮৪)। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
গণপরিষদে সবচেয়ে বেশি সরব
সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের মধ্যে যে কয়কজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, আসাদুজ্জামান খান তাঁদের অন্যতম। একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে বঙ্গবন্ধু তাঁকে এই কমিটিতে যুক্ত করেছিলেন। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যের কমিটির গঠনের আগে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য যে চার সদস্যকে নিয়ে চেয়ারম্যানের তালিকা ঘোষণা করা হয়, তার এক নম্বরেই ছিলেন আসাদুজ্জামান খান। এই কমিটিতে আরও ছিলেন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য দেওয়ান আবুল আব্বাস। বাকি দুই সদস্য হলেন এ বি এ মকছেদ আলী এবং নূর জাহান মুরশিদ।
এদিন মনসুর আলীর প্রস্তাবমতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য যে ৩৪ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়, আসাদুজ্জামান খান ছিলেন সেই তালিকার ১৭ নম্বরে। অধিবেশনের শুরুর দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সংবিধানের খসড়া থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন আসাদুজ্জামান খান। মূলত সংবিধানের নানা অনুচ্ছেদ, দফা ও উপদফা নিয়ে তিনিই সবচেয়ে বেশি কথা বলেছেন। ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর বাইরে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি কথা বলেছেন কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

২০২০ সালে আসাদুজ্জামান খানের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর ভাইয়ের ছেলে কাজী শাহীন
প্রসঙ্গত, ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিলের পরে গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায় এবং পুনরায় অধিবেশন শুরু হয় ওই বছরের ১২ অক্টোবর। এদিন অধিবেশনের শুরুতেই প্যানেল চেয়ারম্যান বা সভাপতিমণ্ডলির তালিকা ঘোষণা করেন স্পিকার। ১১ এপ্রিল যে চারজনকে নিয়ে প্যানেল অব চেয়ারমেন গঠন করা হয়েছিল, সেই চারজনই বহাল থাকেন। এরপর এদিনই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি রিপোর্টসহ খসড়া সংবিধান সম্পর্কে একটি বিল পেশ করেন আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলি এবং সংবিধান প্রণয়ন-মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।
সংবিধান বিলের ওপর দীর্ঘ আলোচনা
সংবিধানের খসড়া বিল পরিষদের উত্থাপনের ১২ দিন পরে ২৪ অক্টোবর আলোচনায় অংশ নেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি শুরুতে বলেন, আজকে যে সংবিধান আমরা দিতে যাচ্ছি, সেই সংবিধানকে এই গণপরিষদের সদস্যদের নিজস্ব সংবিধান মনে করলে ভুল করা হবে। কেননা গণপরিষদ কী, সেই সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। গণপরিষদ সমগ্র জাতির পরিষদ। অর্থাৎ বাংলার সকল মানুষই নিজেদের জন্য এই সংবিধান রচনা করছেন। আমরা তাঁদেরই প্রতিনিধিত্ব করছি।
সংবিধান বিল পাশ করার আগে এর ওপর জনমত যাচাইয়ের যে প্রস্তাব অনেক সদস্য দিয়েছেন, সে বিষয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন, জনমত যাচাইয়ের অনেক অসুবিধা রয়েছে। কমিটি গঠিত হওয়ার পর সাংবিধানিক রীতি-নীতি অনুযায়ী সংবিধান সম্পর্কে কারও কোনো বক্তব্য থাকলে কমিটির কাছে তা পেশ করতে পারতেন। সেই উদ্দেশ্যে ৮ মে তারিখের পূর্বে সংবিধান কমিটির সচিবের নিকট পরিষদ-ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা- এই ঠিকানায় সকল শ্রেণির নাগরিককে তাঁদের মতামত পাঠানোর জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম। আমরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম যে, তাঁরা কমিটির কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। কমিটির বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এই প্রস্তাব সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হোক। এই আবেদন সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বার বার প্রচার করা সত্ত্বেও কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান কোনো প্রস্তাব পাঠাননি। উপরন্ত কোনো কোনো দল অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে সংবিধান সম্পর্কে সরকার অথবা ক্ষমতাসীন দল কোনো পরামর্শ করেননি। এই অভিযোগ অত্যন্ত অযৌক্তিক। গণতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে যে, সংবিধান সম্পর্কে কারো কোনো বক্তব্য থাকলে গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে হবে।
এদিন সময়ের অভাবে আলোচনা শেষ করতে না পারায় পরদিন ২৫ অক্টোবর বৈঠকের শুরুতেই আলোচনা শুরু করেন আসাদুজ্জামান খান। এদিন তিনি খসড়া সংবিধানের ওপর দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বক্তৃতা দেন এবং সংবিধানের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ নিয়ে সদস্যদের বক্তব্যের জবাব দেন। কিছু বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যা দেন। কেন এই বিধানগুলো সংবিধানে যুক্ত করা হলো, সেটি পরিষ্কার করেন।
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নের জবাব
প্রধানমন্ত্রীকে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে—এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আসাদুজ্জামান খান বলেন, সংবিধানে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আপনারা চাইবেন, অথচ প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা গণতন্ত্রে স্বীকৃত, তা তাঁকে দেবেন না, এটা হতে পারে না।
তিনি বলেন, ‘কোনো পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে, জনগণের কাছে যাওয়া দরকার, তাহলে তাঁকে বাধা দেওয়ার বিধান কোনো পার্লামেন্টে নাই, কোথাও নাই। এবং প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা থাকতে হবে। এটা তাঁর অধিকার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।’
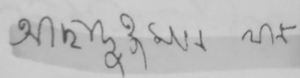
সংবিধানে আসাদুজ্জামান খানের স্বাক্ষর
যখন কোনো দল ক্ষমতায় না থাকে, তখন তাদের একটা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণ জানেন যে, তাঁদের সামনে দুজন প্রধানমন্ত্রী আছেন- একজন সরকারে অধিষ্ঠিত আর একজন সরকারের বাইরে। এবং জনগণ যখন কোনো দলকে সরকার গঠনের জন্য ভোট দেন, তখন তাঁদের মনে থাকে, এই দলের নেতা কে হবেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। প্রধানমন্ত্রীর উপর তাঁরা একটা আস্থা স্থাপন করেন। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর বিশিষ্ট স্থান মেনে নিয়ে জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করবার বিধান আমরা করেছি।
প্রসঙ্গত, ২৭ অক্টোবরের বৈঠকে খসড়া সংবিধানের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পরিষদের মহিলা আসনের সদস্য বদরুন্নেসা আহমেদও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশি দেওয়া হয়েছে—এমন সমালোচনার জবাবে বলেন, ‘যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা হ্যারল্ড লাস্কির পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্ট ইন ইংল্যান্ড নামক পুস্তকে দেখতে পাবেন যে, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা জার্মান সম্রাট এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি; কিন্তু তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। প্রধানমন্ত্রী সংসদের কাছে দায়ী এবং সংসদ জনগণের কাছে দায়ী। সুতরাং, প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা দেওয়ার মানেই জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া।’ (গণপরিষদ বিতর্ক, পৃ. ৩৭৯)।
মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যা
সংবিধানের মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হলে আসাদুজ্জামান এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘মূলনীতিগুলির মধ্যে যে সমস্ত অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি এই সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে। বস্ত্রের দাবি, অন্নের দাবি, কার্যের সংস্থান, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মৌলিক দাবি মূলনীতিগুলির মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এই দাবিগুলির মধ্যে যেগুলি আইনের মাধ্যমে সম্ভব, সেগুলিকে বর্তমান পর্যায়ে বলবৎযোগ্য করা সম্ভব, সেগুলিকে এই সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
যে সমস্ত অধিকারের কথা আমরা মূলনীতিতে বলেছি, সেগুলিরও স্বীকৃতি আমরা দিয়েছি স্পষ্ট ভাষায়, দ্ব্যর্থহীনভাবে। মৌলিক অধিকারের বেলায় একমাত্র তফাৎ যে, মৌলিক অধিকার যেগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যদি রাষ্ট্রের কোনো নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা পার্লামেন্ট বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ খর্ব করে বা খর্ব করে কোন কার্য করে অথবা পরিষদে কোনো আইন প্রণয়ন করে, তাহলে সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনো আইন-দ্বারা বা কার্য-দ্বারা সেগুলিকে খর্ব করা যাবে না।
আর মূলনীতির কথা হচ্ছে যে, নীতিগুলি হবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য। যদিও এইগুলি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়, তবু রাষ্ট্র সর্বদাই এই নীতিগুলির বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকবেন এবং মূলনীতিতে স্থিরীকৃত অধিকারগুলিকে যদি আইনত বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিভিন্ন পর্যায়ে সে সমস্ত অধিকারের নিশ্চয়তাবিধান করতে হবে। যখনই সম্ভব হবে, তখনই মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে এই নীতিগুলির গ্যারান্টি দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে ঐরূপ নিশ্চয়তা দিতে গেলে সেটা হাস্যকর এবং অযৌক্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।’
তিনি বলেন, মূলনীতিভুক্ত যে সমস্ত অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব, যেগুলি মানুষের জন্মগত অধিকারের অন্তর্গত এবং মানুষের ভোগ করা উচিত, আমরা সেগুলিকে মৌলিক অধিকারভুক্ত করেছি। বিভিন্ন মৌলিক অধিকার- ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি যাকে বলা হয় civil liberty- সেগুলির নিশ্চয়তাবিধান আমরা করেছি সেগুলিকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এই পর্যায়ে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সেটা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে এবং সেইভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে, আমরা অন্যায় করেছি, না ঠিকই করেছি। ওইগুলি আমরা মৌলিক অধিকারভুক্ত করি নাই। কেন করি নাই, সেটা আজকে দেখতে হবে।
প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য না করা, সরকারে নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ, জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার।
তবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন—যাতে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ; কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার; বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার অর্জন নিশ্চিত করা যায়।
বিচারক নিয়োগ-সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে সংশোধনী
উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়াগ-সম্পর্কিত সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে একটি সংশোধনী আনা হয় আসাদুজ্জামান খানের প্রস্তাবে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য এই যোগ্যতাগুলো শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হয়। ১. অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করা। ২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে দশ বছর কোনো বিচার-বিভাগীয় পদে থাকা। ৩. কমপক্ষে তিন বছর জেলা-বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করা।
আসাদুজ্জামান খান বলেন, জজ-নিয়োগের বেলায় ‘বার’ থেকে যদি নিয়োগ করা হয়, তাহলে অন্যূন দশ বৎসর অ্যাডভোকেট থাকার দরকার। এ ধরনের যাঁরা হাইকোর্টে দশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন, অথবা দশ বছর জেলা-জজের পদে ছিলেন তাঁরাই হাইকোর্টের জজ হতে পারবেন।
তিনি দাবি করেন, এই সংশোধনী যদি গ্রহণ না করা হয়, তাহলে যাঁরা বাইরে থেকে আসবেন তাঁরা কোনোদিনই হাইকোর্টের জজ হতে পারবেন না। যাঁরা জেলা জজের পদে অধিষ্ঠিত থাকেননি, এরকম কোনো লোক যদি বাইরে থেকে, মফস্বল থেকে আসেন, তাহলে তাঁরা কোনোদিনই হাইকোর্টের জজ হতে পারবেন না। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই আমি এই সংশোধনী এনেছি।
এরপর আইন ও সংবিধান প্রণয়ন-বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই সংশোধনী গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা, উকিলদের মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে, সেটা এতে দূর হবে। এখানে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা দুইভাবে করা হয়েছে। একভাবে ‘বার’ থেকে, অন্যভাবে জেলা-জজদের মধ্য থেকে। এই সংশোধনী ছাড়া তাঁদের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভে অসুবিধা হবে। তাই অন্য সংশোধনী গ্রহণ করে এটাও গ্রহণ করা উচিত। এ সময় স্পিকার সংশোধনীটি ভোটে দিলে তা কণ্ঠভোটে পাশ হয়।
প্রসঙ্গত, বাহাত্তরের মূল সংবিধানে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়েগে এরকম বিধান করা হলেও পরবর্তীতে অবশ্য কমপক্ষে তিন বছর জেলা-বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বাদ দেয়া হয়। অর্থাৎ এখন বিচারক নিয়োগের যে বিধান, তাতে কোনো আইনজীবীর জেলায় বিচারক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি বিচারক হতে পারবেন।
নোট অব ডিসেন্ট
সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কমিটির যে ছয়জন সদস্য সংবিধান বিলের ওপর যে মতানৈক্যমূলক বক্তব্য বা ভিন্নমতসূচক আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) দিয়েছিলেন, আসাদুজ্জামান খান তাঁদের অন্যতম। নোট অব ডিসেন্ট প্রদানকারী বাকি পাঁচ সদস্য হলেন হাফেজ হাবীবুর রহমান, এ কে মুশাররফ হোসেন আকন্দ, আব্দুল মুন্তাকীম চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল।
আসাদুজ্জামান খান খসড়া সংবিধানের ৪২ এবং ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে যে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করেন, সেটি এরকম:
অনুচ্ছেদ ৪২: এই অনুচ্ছেদে কার্যত এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীনভাবে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে না।
প্রতিটি দেশে লিখিত সংবিধান দ্বারা নাগরিকদের কিছু ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা করা হয়। এসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে। কারণ সাধারণ অধিকার আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু মৌলিক অধিকার সংবিধান সংশোধনী ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া এসব অধিকার স্থগিত বা খর্ব করাও যায় না।
পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন, ভোগ এবং হস্তান্তর করা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এসব সংবিধানে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে জনস্বার্থ ছাড়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করার কোনো আইন ছাড়া কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র নিতে পারবে না।
সমাজতান্ত্রিক দেশেও, যত অল্প পরিসীমাতেই হোক না কেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সংবিধান দ্বারা রক্ষা করা হয়। পূর্ব জার্মানির সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলো এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।
অনুচ্ছেদ ১১(১): নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার উত্তরাধিকারদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো।
অনুচ্ছেদ ১৬: শুধু আইনের ভিত্তিতে জনস্বার্থে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাবে।
কাজেই এটা দেখা যাবে যে গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যেকোনো দেশেই হোক, সংবিধান এই নিশ্চয়তা দেয় যেকোনো ব্যক্তির সম্পত্তি জনস্বার্থ রক্ষা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ছাড়া নেওয়া যায় না।
খসড়া সংবিধানের বিধানগুলো এ দুটি রক্ষাকবচ ছাড়াই রাষ্ট্র কর্তৃক কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই রক্ষাকবচগুলোর অনুপস্থিতিতে পার্লামেন্ট কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনো নাগরিকের সম্পত্তি নিয়ে নেওয়াকে বৈধতা দেওয়ার মতো আইন ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারবে। ফলে (১) দফায় প্রদত্ত নিশ্চয়তা পুরোপুরি নাকচ হয়ে যাবে।
খসড়ায় এই বিধানের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে ক্ষতিপূরণসহ নাকি এটি ছাড়াই বা জনস্বার্থ ব্যতিরেকে সম্পত্তি অধিগ্রহণ অনুমোদন করা হবে এ বিষয়টি ঠিক করার ভার ইংল্যান্ডের মতো করে আমাদের এখানেও আইনসভার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই যুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। এটা গ্রহণ করা হলে মৌলিক অধিকার-সংবলিত সংবিধানের তৃতীয় ভাগ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আগে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার, যা শুধু শাসন বিভাগ কর্তৃক লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করা হয়েছে তা নয়, আইন বিভাগ (পার্লামেন্ট) কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেও এর লঙ্ঘন করা যাবে না। কারণ, পার্লামেন্ট শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের অস্থায়ী ইচ্ছের প্রতিনিধিত্ব করে এবং এটি মুহূর্তের আবেগে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে কোনো ভুল করে ফেলতে পারে। আর ইংল্যান্ডের উদাহরণ এখানে অনুপযুক্ত। ইংল্যান্ডের সংবিধান হচ্ছে অলিখিত এবং সেখানে লিখিত সংবিধানের মতো করে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ নয়। অধিকন্তু সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর জনগণের অসীম আস্থার ওপর ভিত্তিশীল এবং সেখানে জনস্বার্থে ছাড়া ও ক্ষতিপূরণ ব্যতীত পার্লামেন্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণের আইন করেছে, এমন কোনো নজির নেই।
এসব বিধানের পক্ষে এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে পার্লামেন্টের এমন ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে আমাদের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে না। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে, সংবিধানে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি।
এটি পুরোপুরি স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে আমি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার বিপক্ষে নই। আমি জানি, এ জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরের ব্যক্তি সম্পত্তিকে আইন দ্বারা জাতীয়করণ করার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তির অধিগ্রহণ সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। এটি অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণির ওপর প্রভাব ফেলে এবং আবার একই সঙ্গে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তিতে মালিকানা থাকতে পারত, এমন ব্যক্তিদেরও বঞ্চিত করে। জাতীয়করণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি তাই শুধু ব্যক্তি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হবে না, এ বিষয়টি বরং আইনসভার ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।
আমি জোর দিয়ে যা বলতে চাই, যতটুকু সম্পত্তি আইনগতভাবে কোনো নাগরিক মালিকানায় রাখতে পারবে, তার চেয়ে অল্প কিছু বেশি সম্পত্তি থাকলে তা রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংবিধানে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, জনস্বার্থে ছাড়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের আইনানুগ ব্যতীত এটি করা হবে না। এই নিশ্চয়তা খুব প্রয়োজন। কারণ, সংবিধান নাগরিকদের কাজ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে ভরণপোষণের অধিকার বা অসুস্থতা ও ডিজঅ্যাবিলিটির ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়নি, যা সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে দেওয়া হয় এবং তার ও তার পরিবারের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টি এখানে নাগরিকদের নিজস্ব সক্ষমতা ও সম্পত্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
অনুচ্ছেদ ৭০
সংবিধানে এর অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে আমার স্পষ্ট আপত্তি রয়েছে। এতে কোনো ব্যক্তিকে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে কোনো উপযুক্ত তদন্ত বা তার বক্তব্য শোনার বিধান নেই বলে কোনো সদস্য দলের ভেতরের কোন্দল বা হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে পারেন। এটি সব গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী, ভোটারদের অধিকারের লঙ্ঘন এবং এতে দলের সদস্যদেরকে, বিশেষ করে সরকারের উচ্চ পদে থাকা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আজ্ঞাবাহী করে তুলবে।
এটি সংবিধানে রাখতে হলে স্বেচ্ছাচারমূলক বহিষ্কারের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। দল থেকে বহিষ্কারের পূর্বে দলের সদস্যকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটি জানাতে হবে, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে এবং অভিযোগটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। অধিকন্তু সাব- আর্টিকেল ৩-এর অধীনে কোনো সদস্য নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন করলে পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, যাতে তিনি বিচার করে দেখতে পারেন এসব শর্ত ঠিকমতো পালন করা হয়েছে কি না। (আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২, প্রথমা/২০২২, পৃ.১৭৭)।
বাহাত্তর-পরবর্তী জীবন
১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ময়মনসিংহ-২৬ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৮৩৫ জন। আসাদুজ্জামান খান পেয়েছেন ৪০ হাজার ৫৩ ভোট।
১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরকারের পাটমন্ত্রী নিযুক্ত হন আসাদুজ্জামান খান। একই বছরের ফেব্রুয়ারিতে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে তিনি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারে যোগ দিয়ে তিনি বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যায়।
১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৮ আসন থেকে তিনি আওয়ামী লীগের (মালেক) প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৯৮ জন। আসাদুজ্জামান খান পেয়েছেন ১৮ হাজার ২১৪ ভোট। প্রসঙ্গত, এই আসনে তিনজন প্রার্থীর ভোট ছিল কাছাকাছি। যেমন আসাদুজ্জামান খানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আশরাফ উদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ১৭ হাজার ৯৭২ ভোট। অর্থাৎ আসাদুজ্জামান খান জয়ী হয়েছেন মাত্র ২৪২ ভোটের ব্যবধানে। আর তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক জালাল উদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ১৩ হাজার ৬৬৭ ভোট। (বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও ফলাফল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯)।
১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসস নির্বাচনের জয়ী হওয়ার পরে আসাদুজ্জামান খান আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা এবং সেইসাথে সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত তিনি উভয় পদে দায়িত্ব পালন করেন।
সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর বিরোধিতা
জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে প্রশ্ন ওঠে যে, যেহেতু রাষ্ট্রের লাভজনক পদে থাকা কেউ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন না এবং উপরাষ্ট্রপতি পদটি লাভজনক কি না, সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা নেই, অতএব আব্দুর সাত্তার নির্বাচনে অংশ নেয়ার যোগ্য নন। এ নিয়ে সংসদে এবং সংসদের বাইরে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলে। বলা হয়, জিয়ার মৃত্যুর পরে সৃষ্ট শূন্যতায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য বিচারপতি সাত্তার ছাড়া বিএনপির আর কোনো যোগ্য প্রার্থী ছিলেন না। উপরন্তু সাত্তারকে বিএনপির প্রার্থী করার পেছনে তৎকালীন সেনা প্রধান এইচ এম এরশাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলেও শোনা যায়। এমতাবস্থায় বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সুযোগ দিতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়।
১৯৮১ সালের ৮ জুলাই সংবিধান সংশোধনী কমিটি পুনরায় বৈঠকে বসে এবং লিখিতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, উপরাষ্ট্রপতির পদটি হবে নির্বাচিত একটি পদ এবং মৃত্যুজনিত বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির মেয়াদের বাকি সময়ের জন্য উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ সময় প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে যে, উপরাষ্ট্রপতি সংসদ দ্বারা নির্বাচিত হলে উক্ত অবস্থায় তা হবে সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কারণ সংবিধানে বলা হয়েছে যে, দেশের রাষ্ট্রপতি হবেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এই ইস্যু এবং আরো কতিপয় বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে অনুভূত হয় যে, সংশোধনী বিল চূড়ান্ত করার জন্য আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরশাদের চাপের কারণে এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভিন্নধর্মী দল শেষ পর্যন্ত এই শর্তে বিলটি পাস করাতে সম্মত হয় যে, উপরাষ্ট্রপতির ইস্যুটি নিষ্পত্তির জন্য সপ্তম সংশোধনী বিল আনার লক্ষ্যে ১০ দিনের জন্য সংসদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হবে। এদিনই, অর্থাৎ ৮ জুলাই বিচারপতি সাত্তার যাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারেন, সেজন্য বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী বিল অনুমোদিত হয়।
এ সময় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্বে ছিলেন আসাদুজ্জামান খান। সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করার সুযোগ দেয়ার বিরোধিতা করে তিনি এদিন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সারা জাতির স্বার্থে নয়, একক একজন ব্যক্তির স্বার্থে এই বিল পাস করানো হয়েছে। তিনি বিলটি পাস করানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন এজেন্সী কর্তৃক সংসদ সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগও উত্থাপন করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ জুলাই ১৯৮১)।
ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন
আসাদুজ্জামান খানের স্ত্রী জামসেদুন্নেসা ছিলেন রাজধানীর টিকাটুলিতে অবস্থিত কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক হিসেবে এই স্কুল থেকে তিনি অবসরে যান। আসাদুজ্জামান জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি মারা যান। এই দম্পতি নিঃসন্তান।
আসাদুজ্জামান খান শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯৮৬ সালের পরে আর রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। শেষদিকে আইন প্র্যাকটিস করতেন বাসায় বসেই। জুনিয়ররা বাসায় এসে পরামর্শ করে যেতেন।
এই প্রবীণ আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ দেশের অনেক শিক্ষা ও ক্রীড়া সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ায় বিভিন্ন সম্মেলন উপলক্ষ্যে ব্যাপক সফর করেছেন। কাজী শাহীন জানান, তাঁর (আসাদুজ্জামান খান) তোপখানা রোডের বাড়িতে হাইকোর্টের চেয়েও সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি ছিল। হাজার হাজার বই ছিল—যার বড় অংশই আইনবিষয়ক। তিনি প্রতিবার বিদেশ থেকে প্রচুর বই নিয়ে আসতেন। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি একা হয়ে যাওয়ায় পাশেই তাঁর মামাতো ভাই শিল্পপতি জহুরুল ইসলামের বাসায় থাকা শুরু করেন। এ সময় বাড়ি থেকে বইপত্র চুরি হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাড়িটা বিক্রি করে দেয়া হয়।
আসাদুজ্জামান খানের সততার উদাহরণ দিতে গিয়ে কাজী শাহীন বলেন, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পরে বিরোধী দলীয় নেতা থাকাকালীন তাঁর একজন এপিএস বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) চাকরির আবেদন করেছিলেন। তখন পিএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন আসাদুজ্জামান খানের ছাত্র। তাঁর এপিএস অনুরোধ করলেন তিনি যেন একটু সুপারিশ করে দেন। কাজী শাহীন বলেন, চাচা কোনোদিন কারো কাগজে এই কথা লেখেন নাই যে, ‘সুপারিশ করা গেলো’। তিনি এপিএসকে বললেন, ‘তুমি যোগ্য ছেলে। আমার সঙ্গে দুই বছর ধরে আছ। ইন্টারভিউ দাও। তোমার চাকরি এমনিই হবে। সুপারিশ করা মানে কিছু ঘাটতি আছে। আমি কেন প্রথম শ্রেণির একটা চাকরির জন্য ঘাটতিসম্পন্ন একজনের পক্ষে সুপারিশ করব?’
অসুস্থতা, মৃত্যু ও দাফন
আসাদুজ্জামান খান দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগেছেন। কাজী শাহীন খান বলেন, ‘চাচারে দেখতাম ঘরের মধ্যে হাঁটে। তখন তো বুঝতাম না যে একটা বৃদ্ধ মানুষ ঘরের ভেতরে একা একা হাঁটে কেন? ভাবতাম কোনো বড় কোনো অসুখ হয়েছে কি না। পরে জানলাম যে ডায়াবেটিক রোগীদের হাঁটতে হয়।’
আসাদুজ্জামান খানের মৃত্যুর তিনদিন আগে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন শাহীন। বলেন, ‘সকালে আসছি। বিকালে চলে যাব। ভাবলাম চাচার সাথে দেখা কইরা যায়। বিকাল বেলা বাসায় গিয়া দেখি মশারি টানানো চলতেছে। চাচারে বললাম, আপনারে কিশোরগঞ্জ নিয়া যাই চলেন। চাচা একটু চুপ থেকে বললেন, তোর ওইখানে তো কমোড নাই।’ অর্থাৎ টয়লেটের বিষয় নিয়ে তখন তিনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। শাহীন বললেন, ‘দুইদিনে কমোড লাগায়ালাম। চাচা কইলো আইচ্ছা। তারপর তো আসলাম লাশ নিতে।’…

কিশোরগঞ্জ শহরে আসাদুজ্জামান খানের বাড়ি সংলগ্ন তাঁর সমাধি
১৯৯২ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি জহুরুল ইসলামের বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন সকালে প্রথম জানাজা হয় সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে। সেখানে বিচারপতি, মন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অং নেন। এখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরগঞ্জ শহরে। আখড়াবাজার এলাকায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে ওইদিনই পারিবারিক কবরস্থানে বাবার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

